কবিতার নতুন প্রস্তবনা বিষয়ে এতো কথা বলার অর্থই হলো কবি হাসনাইন হীরা’র ‘বাঁক বাচনের বৈঠা’ কবিতাগ্রন্থের সুবাদে। কারণ ‘বাঁক বাচনের বৈঠা’ পাঠ করতে হলে পাঠককে অবশ্যই কবিতার নতুন প্রস্তবনাটি পাঠ করতে হবে নাহলে এক ব্যর্থ দোদুল্যমানতার ভেতর দিয়ে পাঠককে বিস্ফোরিত, অনাকাঙ্ক্ষিত, ফলশূন্যের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। মূলত এই প্রস্তাবনার ভেতর রয়েছে কবিতার নন্দনতত্ত্ব বা শিল্পদর্শন। কবি হাসনাইন হীরা এখানে কবি ও দার্শনিক দু-ই। তবে আমি তাঁকে সে হিসেবে খ্যাত করতে চাই না। একটু উল্টে বলতে পারি শব্দতান্ত্রিক। দর্শনধ্যানি। এই প্রস্তাবনার ভেতর দিয়ে কবি হাসনাইন হীরা খুব সতর্কভাবে অন্তর্নিহিত বিবর্তনের পথে চলে গেছেন। সে পথ সীমাহীন পথ। গ্রহণ করার সক্ষমতা থেকে বৃহদাকার মহাশক্তিশালী পথ। তান্ত্রিক যেভাবে কোজাগরী চাঁদকে মর্ত্যে নামিয়ে আনেন, ঠিক তেমনি কবি হাসনাইন হীরা কবিতার নতুন প্রস্তাবনার মাধ্যমে কবিতার নন্দনতত্ত্বকে মর্ত্যে এনে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছেন। এখানে কবি হাসনাইন হীরা নিঃসন্দেহে প্রগতিবাদী কিন্তু তাঁর প্রগতির ভেতর স্বতঃস্ফূর্ত স্বতন্ত্রতা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রস্তাবনার শুরুতেই কবি হাসনাইন হীরা প্রগতিকে প্রকৃতির বিবর্তনবাদের ভেতর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে কবি এড়িয়ে গেছেন যান্ত্রিক প্রগতিকে। তিনি উপলব্ধি করেননি যান্ত্রিক প্রগতিও উদ্দেশ্যমুখী। “ভোরের রোদ, চাঁদের বেহাগ, জোনাকির সংরাগ, কালের তোরণ” এসবকিছুতে দার্শনিকসুলভ যুক্তির উঞ্চতা পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও তা সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ অন্তর্নিহিত প্রবণতা। শব্দ থেকে ক্রমশ ধাবিত হয়েছেন সংকেতের দিকে। তবে স্পষ্টতই সাধারণ বাহ্যজগৎ ও মানবজীবনের ভাব-কল্পনাকে মনোরোম করে তুলেছেন। ভাবকে রূপে পরিবর্তন করেছেন। যা অদেহী, অরূপ, সূক্ষ্ম বা ইন্দ্রীয়াতীত, কবি হাসনাইন হীরা এই প্রস্তাবনার ভেতর দিয়ে রূপ ও ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য মূর্তি দান করেছেন। কবিতার নতুন প্রস্তাবনায় চিরন্তন আবেদনকে আমাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধের কাছে বিমূর্ত করেছেন। ভাবসঞ্চারী বিচিত্র রসকে প্রস্ফুটিত করেছেন অ-নীতিদ্রোহী হয়ে। এ-ধরনের প্রস্তাবনায় যেটি স্পষ্ট প্রতীয়মান তা হলো Rhythm বা ছন্দস্পন্দন। এই ছন্দ স্পন্দনে ভাব ও লয়ের সৌন্দর্য সুষমা। কবিতার নতুন প্রস্তাবনা পাঠে সময়ের গ্রন্থিলতা এবং বাচনিক প্রক্রিয়াকে আধুনিকোত্তর নন্দের সন্ধানী করে পাঠককে অন্তহীন যাত্রার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। এখানে সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক মৌল একককে এমনভাবে প্রচলিত বাস্তবতার আদলে সেলাই করেছেন তা বিছিন্ন হবার নয়। এটাই হলো কবিতার নতুন প্রস্তাবনার ব্যাপারে অর্থবোধক নান্দনিক উৎপাদন ও প্রতীতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
“কোন মাঝির সারগেত আমি? কোন ঘাট চেনা উপকূল? ভাবছি। কাতরাচ্ছি। বাইছি বাচনের বৈঠা” প্রস্তাবনার এই অংশে চরিত্রের স্বভাব ও বাচনভঙ্গিকে তাৎক্ষণিক তৎপরতার সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন। দৃষ্টিভঙ্গিকে এতদূরে থ্রো করেছেন যাতে ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক বিকাশের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র প্রদান করা যায়। এ কথা সত্য যে, শিল্প মতাদর্শের প্রতিফলন করা ছাড়াও সমাজে মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতির সঙ্গে আরো জটিল সম্পর্ক বজায় থাকে। এরপরেও শিল্পরূপজ্ঞান না থাকলে কোনো সৃষ্টি কিংবা নীতি সুষম, সুন্দর হতে পারে না। সবকিছুরই Supremely real এর প্রতিধ্বনি আছে যা নিষ্প্রয়োজনকে অন্তরের প্রতীতি বা প্রত্যয়-ই শিল্পের জন্ম দিয়ে থাকে। পরিমাণ ও পরিমাপ প্রকাশ রূপেই সুন্দর। প্রস্তাবনার উক্ত অংশে সৌন্দর্য-বিধায়ক শক্তিকে সেভাবেই প্রয়োজনীয় করে তোলা হয়েছে। কবি হাসনাইন হীরার এই প্রস্তাবনার সুবাদে যেমন তান্ত্রিকতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি আত্মকেন্দ্রিক উদাত্ত কল্পনার প্রতিভূ হিসেবে আবিষ্কার করেছেন।
নতুন কবিতার প্রস্তাবনা বিষয়ে লেখা হয়েছে…. “ স্বাধীনতা এক ‘বিনুনিবিতান’। যে কেউ নিতে পারে— নিক। নেওয়াটা আবশ্যিক।” এখানে উপলব্ধি করতে পারা যায় কবি হাসনাইন হীরা অস্তিবাদ মূর্ত মানুষের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য যেকোনো মূল্যে বদ্ধপরিকর। অস্তিবাদ কোনো বস্তু বা বস্তুসামগ্রীর দর্শন নয়। এ হলো মনুষ্য-পরিস্থিতির দর্শন। এ দর্শন বিষয়ীর দর্শন, বিষয়ের দর্শন নয়। কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকে ভেঙে সামনে এগিয়ে যেতে পারলেই কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব। সেটাকে কবি হাসনাইন হীরা কবিতার নতুন প্রস্তাবনার ভেতর জুড়ে দিয়ে কর্কশ ও মধুর জটিলতর প্যাটার্ন আবিষ্কার করেছেন। ঘাত-প্রতিঘাতের ধ্বনিগতরূপ এখানে সিলেবল গঠন করে নিরবচ্ছিন্ন অবস্থানে অবস্থান করছে। মোদ্দাকথা Freedom is every where, কবি হাসনাইন হীরা প্রস্তাবনায় সেটাকেই তুঙ্গে তুলেছেন বেশি করে। নিষ্কর্ষ ও বহির্ভূত অতিরিক্ত বাচনের স্থান দেননি। রচনাপ্রকরণকে জিজ্ঞাসার ভেতর দিয়ে দশদিগন্তের দিশা দেখিয়েছেন। উপলব্ধি করিছেন এই প্রস্তাবনা আধুনিকোত্তর নন্দনের মুখে অভিনব ইশতেহার। উত্তেজনা হতে পারে। উত্তেজিত করাই কবি হাসনাইন হীরার মূল টার্গেট। সঞ্চরমান উপলব্ধির বয়ান যেখানে একবার আঘাত করে সেখানে বিনির্মাণকে অনায়াসে স্বাগত জানানো হয়। এই অভিব্যক্তির কারণেই কবিতার এই নতুন প্রস্তাবনাকে আমি দুর্জয় উত্তেজনার স্মারক হিসেবে ঘোষণা করছি। আরও স্বীকার করছি দশদিগন্ত পার হলেই সমতল, ধীরপায়ে হাঁটা।
কবিতায় চিন্তার থ্রো কতদূর পর্যন্ত করা যায়? এর কি কোনো লিমিট আছে? সীমানা আছে? কিংবা কোনো সতর্কীকরণ আছে? জানা নেই। তবে জীবনোৎকণ্ঠা পরিমাণ যত বেশি কবিতায় ততবেশি চিন্তার থ্রো করা যায় বলে জানি। চিন্তার কোনো অ্যাক্রস্টিক হয় না। হয় না ডেকাডানস্ এর নির্দিষ্ট পরিমাপ। পক্ষান্তরে কথিত আছে, কবিতার টার্ম দ্বারা সেইসব বস্তুকে বোঝায় যা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়। এ প্রসঙ্গে সত্যটিই হলো, যে পাঠক যত ক্লান্ত গোষ্ঠীচেতনার কবিতা পড়ে, সে পাঠক তত চলে যায় কবিতার বাইরে। মূলত সেইসব পাঠককে ধরে আনতে হবে কবিতার মাঝে। কবিতাকে আঁধারের ভেতর দিয়ে পথ খুঁজে পৌঁছাতে হবে মানুষের প্রাণের মাঝখানে। আমাদের হারিয়ে যেতে হবে অপরিচিতের ভীড়ে, যাঁরা হঠাৎ একদিন পথ থেকে তুলে নেবেন, ধুলোবালি সরিয়ে দু’হাতে আদর করবেন অথবা হাজার হাজার বছর ধরে যে সকল ঝরাপাতা অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে তার ভেতর থেকে প্রাণের বস্তুকে খুঁজতে হবে অতি সন্তর্পণে। এ্যানথলজির বাইরে গিয়ে এ্যানালজিকে প্রাধান্য দিতে হবে। শব্দের বর্ণানুক্রম পরিবর্তন করে যেমন নতুন শব্দ তৈরি করা যায় ঠিক তেমনি এই এ্যানাগ্রামের মতোই কবিতার আদি ও অন্তহীন পরাবর্তকে প্রচণ্ড প্রেশার দিতে হবে। তবেই দেখা যাবে কিংবা উপলব্ধি করা যাবে কবিতায় চিন্তার থ্রো কতখানি কত স্পিডে চলে গেছে।
কবি হাসনাইন হীরা তার ‘বাক বাচনের বৈঠা’ কাব্যগ্রন্থে দু’টি বিষয়কে রত্নকোষাগারের মতোই আগলে রেখেছেন:
(১) বিশুদ্ধ কবিতা লেখার আকাঙ্খা।
(২) অবচেতনার জগৎ থেকে সত্যকে দেখতে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা।
বোহেমিয়ানিজম থেকে যদি সমালোচনা করা যায় তবে এর অর্থ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা মুশকিল। তবে মুহূর্তকে বিদায় ও মুহূর্তকে শ্রেষ্ঠ করার আয়োজনে জটিলতম, সূক্ষ্মতম ও কুশলতম মননের প্রয়োগ বোহেমিয়ানিজমের মুন্সিয়ানা সচেতনভাবে সমালোচনায় এনেছেন কবিতায়। তবে আমার স্পষ্ট মনে হয়েছে ‘বিনোদবিহার’ কবিতাটি সার্বিকভাবে মৌলিক হয়নি কারণ এখানে পরম্পরা বা কনভেনশনকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারেননি তিনি। টার্নিং পয়েন্টে নিজ থেকে নিজেকে হাজির করা কিংবা পরিকল্পিতভাবে কিংবা ক্যানোনাইজ করে মূল প্রতিষ্ঠায় পৌনপুনিকতার যথেষ্ট কারণ ছিলো না। তারপরও এটা সত্য যে, “সাধারণত, সঠিক শব্দ খুঁজে পাওয়া ও তাদের এমনভাবে গ্রন্থিত করা যাতে কম সংখ্যক শব্দের দ্বারা গভীর ও পর্যাপ্ত ভাব করা যায়, যাতে শব্দ দিয়ে জীবন্ত চিত্রের সৃষ্টি করা যায় ও চরিত্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তীক্ষ্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় এবং পাঠকের মনে চিত্রিত চরিত্রের স্বভাব ও বাচনভঙ্গি তাৎক্ষণিক তৎপরতার সঙ্গে গেঁথে দেয়া যায়, সে কাজ সত্যি সত্যিই দুরূহ।” যেমনটি বলা হয়েছে কবিতার প্রস্তাবনায় সেই সূত্র ধরে এগোলে বোঝা যাবে, ‘দশঘরার বিনুনিবিতান’ কবিতার কবিতা গঠনের ক্ষেত্রেও এক বিশিষ্টতা রয়েছে। যেখানে গঠনের কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। কবি প্রয়োজনও বোধ করেননি। আয়োজন করেছেন শুধু আলোর ঝলক আনার শৈলি। কবি এখানে পাঠকের কথাও ভাবেননি। নিজেকেই পাঠকের স্থানে বসিয়ে নিজেরই উপর পরীক্ষা চালিয়েছেন। কীভাবে, কত সহজে, কত সংক্ষেপে, নতুনভাবে নিজেই নিজেকে বারে বারে শিহরিত করা যায়! তেমনটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে রূপ কবিতার অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে। যার কারণে পাঠকের কাছে এই রূপনিহন যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কবিতার গুণ হচ্ছে তার উজ্জ্বল পরিবর্তন তৈরি করা। গুণকে আঘাত না করলে যেমন চেনা যায় না গুণাঘাত কি! এখানেই কবির মনোভঙ্গি স্বতন্ত্র হয়েছে।
(১) বিশুদ্ধ কবিতা লেখার আকাঙ্খা।
(২) অবচেতনার জগৎ থেকে সত্যকে দেখতে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা।
কবিতায় তিনি ব্যক্তির আত্ম ও অপরকে অন্তরমন ও বাহির দ্বারা একসঙ্গে বেঁধেছেন। সেখানেই তিনি চিন্তার থ্রো’কে ব্যাখ্যাতীত বিমূর্ততা ও সৌন্দর্যের দিকে ধাবমান করেছেন। মূলত এটাই কবিতার যাবতীয় চিত্রকল্প নামে অভিহিত। বেথস অর্থাৎ চরম পতনকে কবিতার ভেতর খুব ধীরে ও সন্তর্পণে হাঁটিয়েছেন। ‘দশঘরার বিনুনিবিতান’ ভাগে শ্রুতিকটুতা বা স্বরের অনৈক্যকে পরিমিত বোধ ও এ্যানাগ্রামের শৃঙ্খলা দিয়ে রীতিমতো সজোরে থ্রো করেছেন। এই চিন্তার থ্রো-এর উৎপত্তি কীভাবে করেছেন তিনি? খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। মূলত অতিচেতনার মার্গে গমন করে হাসনাইন হীরা বিস্তরভাবে এগিয়ে গেছেন। প্রত্যেক ব্যাপারে সন্দেহ করা, গ্রহণ করা, যাচাই করা, বাস্তবতাকে খোঁজা, বস্তু প্রকৃতি স্বরূপ খোঁজা, বিশ্ব ও বিশ্বব্যবস্থার স্বরূপ খোঁজা, এইসব যাবতীয় এঙ্গেল কবিকে অতিচেতনার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ফ্যান্টাসি বা নতুন থিওরিকে আবিস্কার করার উদ্দেশ্যে নয় বরং নিজের চিন্তার ব্যাপারকে নির্মোহভাবে সময়ের সাথে তাল রেখে এগিয়ে নিয়ে গেছেন কবিতায় কবিতায়। শব্দ ও শব্দের সম্পর্কে জীবনের স্বপ্নের সাথে অস্তিত্বের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন কবিতায়। মগ্নচৈতন্য, অবচেতন বা পরাবাস্তবের মূল পথে না হেঁটে কীভাবে কবিতাকে উদযাপন করা যায়? এমন প্রশ্নের সমাধান টেনেছেন ‘বিনোদবিহার’ কবিতায়। ‘সাধ ও সাধ্যের বাটিতে হেসে ওঠে রোদেলা সারোদ’ কিংবা ‘চেতনাকে লিখে রাখি খ্যাতিমান সারসের ডানায়’ লাইনে পরপর বাস্তবের ইঙ্গিত প্রতীকহীন পরিচিত্রহীন মিথোজকে সম্প্রসারিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সহসাই উচ্চারণ হতে পারে সবচেয়ে কঠিনতম জটিলতম ও মহার্ঘ শিল্প হচ্ছে কবিতা। কেননা এই কবির মনন ও চিন্তনের বোঝাপড়া থেকে বেরিয়ে আসছে বাস্তবতা ও বস্তুগুণ।
বোহেমিয়ানিজম থেকে যদি সমালোচনা করা যায় তবে এর অর্থ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা মুশকিল। তবে মুহূর্তকে বিদায় ও মুহূর্তকে শ্রেষ্ঠ করার আয়োজনে জটিলতম, সূক্ষ্মতম ও কুশলতম মননের প্রয়োগ বোহেমিয়ানিজমের মুন্সিয়ানা সচেতনভাবে সমালোচনায় এনেছেন কবিতায়। তবে আমার স্পষ্ট মনে হয়েছে ‘বিনোদবিহার’ কবিতাটি সার্বিকভাবে মৌলিক হয়নি কারণ এখানে পরম্পরা বা কনভেনশনকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারেননি তিনি। টার্নিং পয়েন্টে নিজ থেকে নিজেকে হাজির করা কিংবা পরিকল্পিতভাবে কিংবা ক্যানোনাইজ করে মূল প্রতিষ্ঠায় পৌনপুনিকতার যথেষ্ট কারণ ছিলো না। তারপরও এটা সত্য যে, “সাধারণত, সঠিক শব্দ খুঁজে পাওয়া ও তাদের এমনভাবে গ্রন্থিত করা যাতে কম সংখ্যক শব্দের দ্বারা গভীর ও পর্যাপ্ত ভাব করা যায়, যাতে শব্দ দিয়ে জীবন্ত চিত্রের সৃষ্টি করা যায় ও চরিত্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তীক্ষ্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় এবং পাঠকের মনে চিত্রিত চরিত্রের স্বভাব ও বাচনভঙ্গি তাৎক্ষণিক তৎপরতার সঙ্গে গেঁথে দেয়া যায়, সে কাজ সত্যি সত্যিই দুরূহ।” যেমনটি বলা হয়েছে কবিতার প্রস্তাবনায় সেই সূত্র ধরে এগোলে বোঝা যাবে, ‘দশঘরার বিনুনিবিতান’ কবিতার কবিতা গঠনের ক্ষেত্রেও এক বিশিষ্টতা রয়েছে। যেখানে গঠনের কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। কবি প্রয়োজনও বোধ করেননি। আয়োজন করেছেন শুধু আলোর ঝলক আনার শৈলি। কবি এখানে পাঠকের কথাও ভাবেননি। নিজেকেই পাঠকের স্থানে বসিয়ে নিজেরই উপর পরীক্ষা চালিয়েছেন। কীভাবে, কত সহজে, কত সংক্ষেপে, নতুনভাবে নিজেই নিজেকে বারে বারে শিহরিত করা যায়! তেমনটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে রূপ কবিতার অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে। যার কারণে পাঠকের কাছে এই রূপনিহন যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কবিতার গুণ হচ্ছে তার উজ্জ্বল পরিবর্তন তৈরি করা। গুণকে আঘাত না করলে যেমন চেনা যায় না গুণাঘাত কি! এখানেই কবির মনোভঙ্গি স্বতন্ত্র হয়েছে।
দুর্জয় খান। কবি ও সমালোচক। জন্ম: ১২ ই অক্টোবর ১৯৯৬, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী। প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ: ‘মানসিক অতৃপ্তির আখ্যান’ (২০২০) ও ‘ছায়াক্রান্তের শব্দানুষঙ্গ’ (২০২১)।
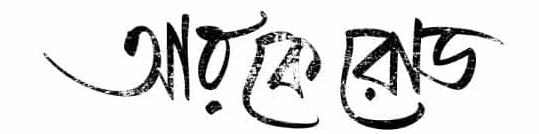
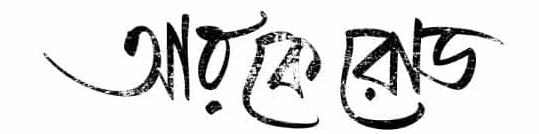
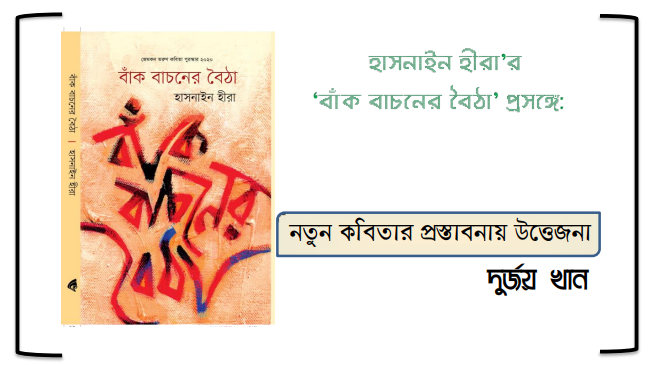












3 মন্তব্যসমূহ
লেখাটা বেশ ভালো লাগল।
উত্তরমুছুনদারুণ। কবিতার লাইন ধরে আলোচনা না করে আত্মাকে তুলে আনার প্রয়াস খুব ভালো লাগল।
উত্তরমুছুনভাল লাগলো গো, বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে গেলাম আর আবিষ্কার করলাম এক অন্য ভাবান্তরের আবেশ।
উত্তরমুছুনমন্তব্যের যাবতীয় দায়ভার মন্তব্যকারীর। সম্পাদক কোন দায় নেবে না।